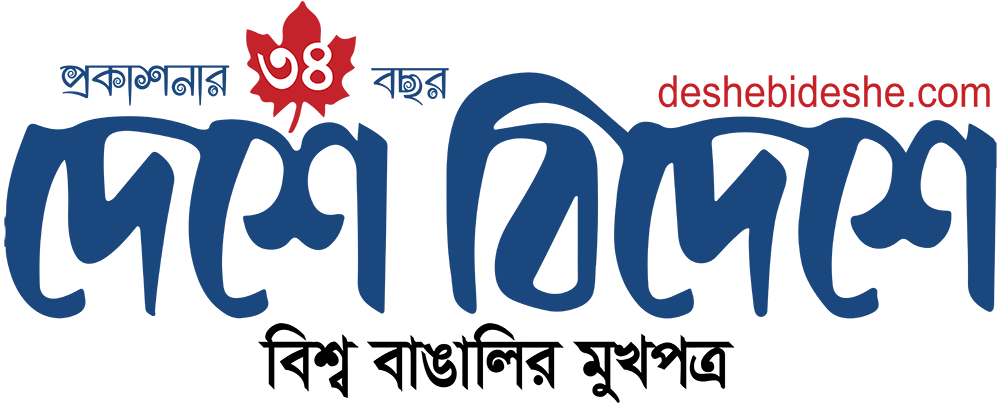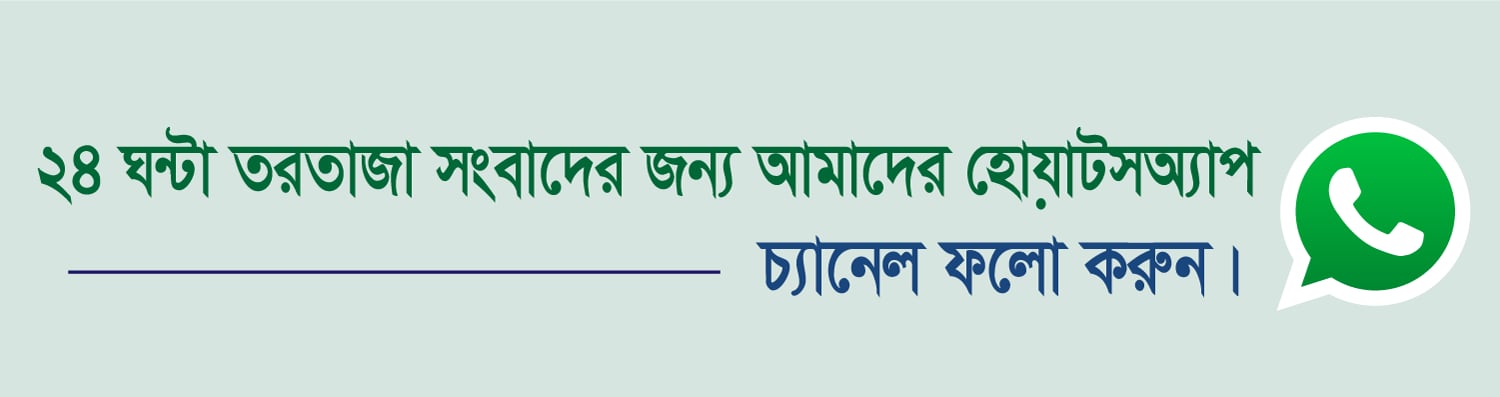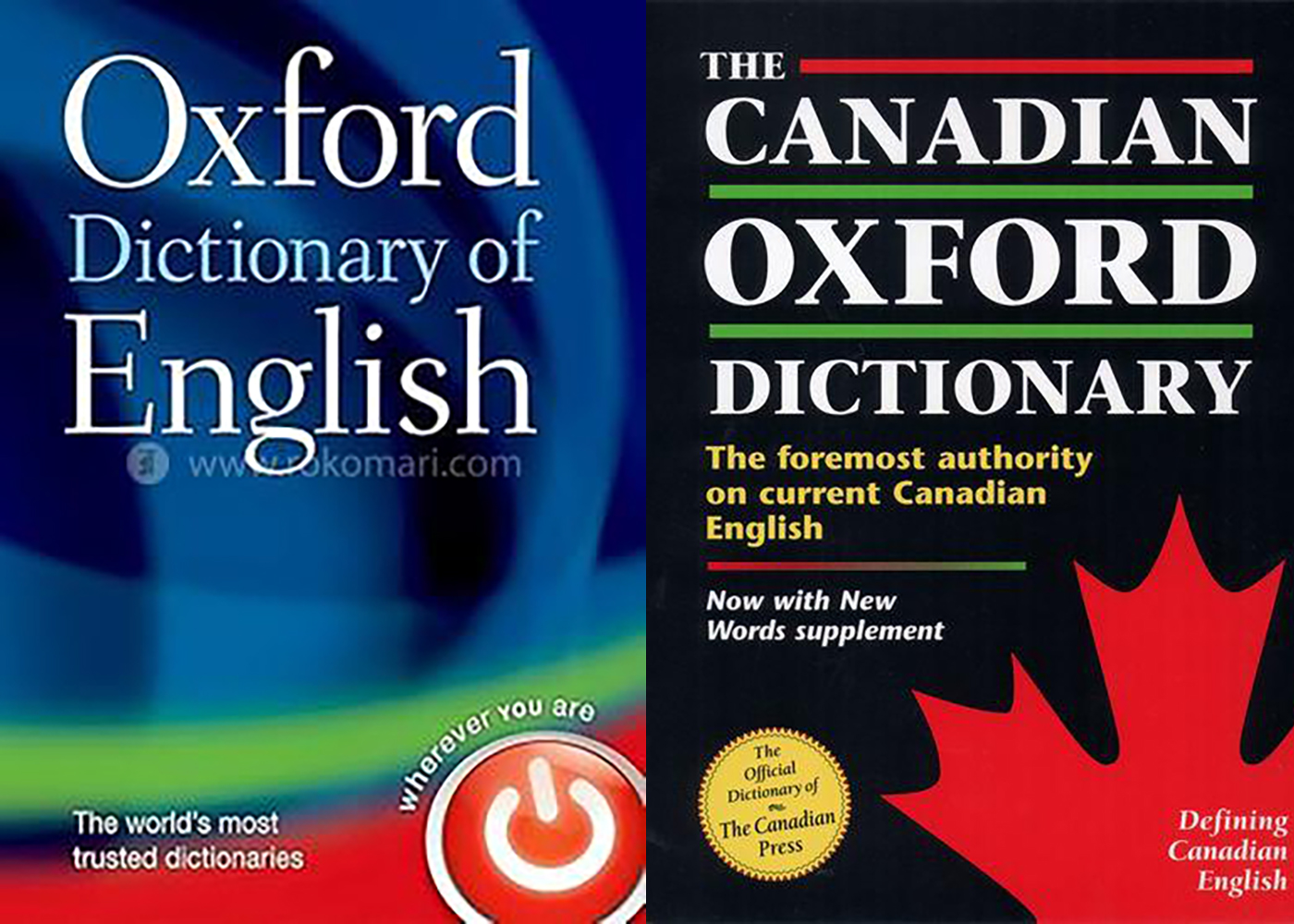
একটি ভাষা-যেটি এককালে রাজ্য শাসন করতো, উপনিবেশ গড়তো, এবং পুরো দুনিয়ার কানে নিজের উপস্থিতি জানান দিতো-আজ নিজেই যেন বিভক্তির শিকার। সেই ইংরেজি ভাষা, যার জন্ম ব্রিটেনের মাটি থেকে, কালের পরিক্রমায় পাড়ি জমিয়েছে আটলান্টিক, অতিক্রম করেছে প্রশান্ত মহাসাগর, আর গিয়ে পৌঁছেছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এমনকি আফ্রিকার সাহারা পেরিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশেও।
কিছু কিছু বিষয় বড়ই বিভ্রান্তিকর। আবার মজাও লাগে। রহস্য ভেদ করতে আরও মজা লাগে। ব্রিটেন, আমেরিকা এবং কানাডা এই তিন দেশের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের নিজস্ব বানানরীতি এমনকি নিজস্ব শব্দও রয়েছে। সর্বোপরি ব্রিটিশ, কানাডা এবং আমেরিকান ইংরেজির আলাদা আলাদা ডিকশনারিও রয়েছে।
একসময় ধারণা ছিল পৃথিবীতে দুই ধরনের ইংরেজি আছে। একটা ব্রিটিশ, আরেকটা আমেরিকান। এরও আগে মনে করতাম ইংরেজি শুধু ব্রিটিশদের। কানাডাতে আসার পর জানতে পারলাম কানাডিয়ান ইংরেজিও আছে। আরও জানলাম, ইংরেজিরও আছে আঞ্চলিকতা, আছে দেশভেদে রীতি, উচ্চারণ, বানান এমনকি শব্দের নিজস্বতা। ব্রিটিশ ইংরেজি, আমেরিকান ইংরেজি, কানাডিয়ান ইংরেজি এবং অস্ট্রেলিয়ান ইংরেজি- এই চারটি বড় ধারাতেই দেখা যায় ভিন্নতা।
ব্রিটিশরা যেখানে বলে ‘colour’, ‘centre’, ‘organise’। আমেরিকানরা সেখানে লেখে ‘color’, ‘center’, ‘organize’। কানাডিয়ানরা ব্রিটিশ বানানই অনেকাংশে বজায় রাখে, তবে উচ্চারণ ও শব্দব্যবহারে আমেরিকান প্রভাব স্পষ্ট।
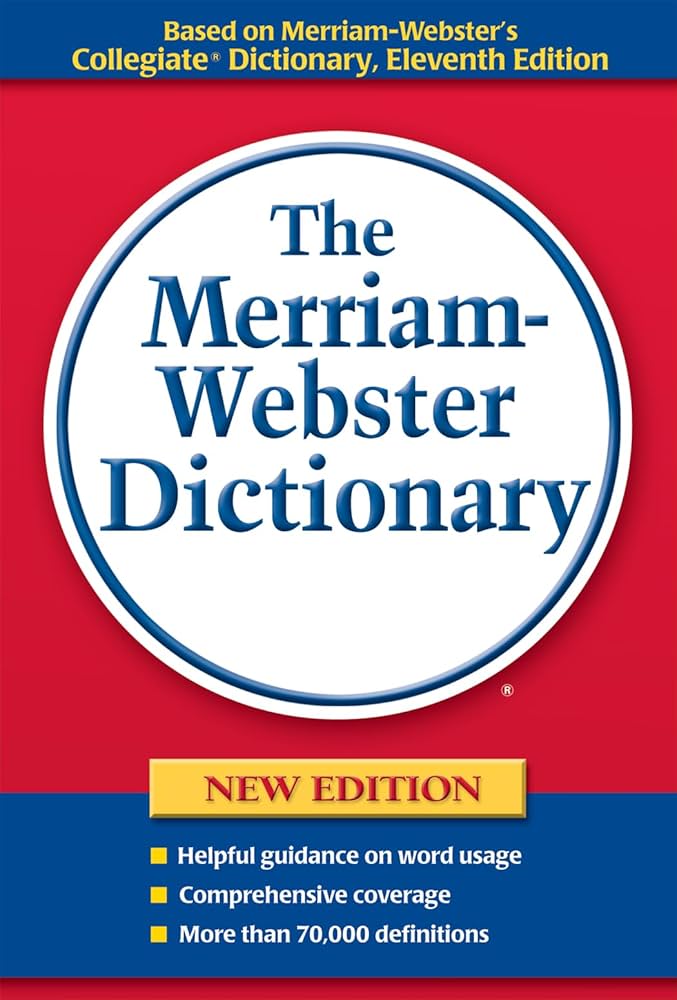
উচ্চারণেও ভিন্নতা বিস্ময়কর। যেখানে আমেরিকানরা বলে schedule (স্কেডিউল), ব্রিটিশরা বলে shedule। আবার advertisement শব্দে বৃটিশরা জোর দেয় শুরুতে, আর আমেরিকানরা জোর দেয় শেষাংশে advertízement।
আরও মজার বিষয়, কেউ বলেন- ‘zee, ’, কেউ বলেন ‘zed’। কেউ বলেন ‘elevator’, কেউ বলেন ‘lift’। একজন বলেন ‘apartment’, তো অন্যজন বলেন ‘flat’।
ব্রিটিশরা যখন biscuit খায়। কানাডিয়ানরা তখন cookie-তে কামড় দেয়। ব্রিটিশরা যখন গাড়িতে petrol ঢালে, কানাডিয়ানরা তখন গাড়িতে gas ভরে, ব্রিটিশরা যখন holiday-তে যায়, তখন কানাডিয়ানরা যায় vacation-এ। ব্রিটিশরা যখন বাচ্চাদের nappy পরায় তখন আমেরিকানরা বাচ্চাদের diaper খুঁজে। Motorway-তে ব্রিটিশরা lorry দেখলে ভয় পায়। আর আমেরিকানরা সাঁ সাঁ হাকিয়ে Highway-তে truck চালায়।
এইসব ছোট ছোট পার্থক্য কখনো হাসায়, কখনো বিভ্রান্ত করে।
কানাডিয়ান অনেক শব্দ আছে যা আমেরিকানদের চাইতেও আলাদা। যেমন, আমেরিকানদের উচ্চারণ হলো ‘জি’, কানাডিয়ানরা বলে ‘জেড’। ব্রিটিশরাও বলে ‘জেড’। আসলে অক্ষরটি তাদের কারোরই নিজস্ব নয়।
কানাডিয়ানরা যেহেতু ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীন ছিল সে জন্য তারা জেডই উচ্চারণ করে। অবশ্য কোনো কোনো কানাডিয়ান আমেরিকান স্টাইলে ‘জি’ও বলে থাকেন। অনেক সময় টেলিফোনে কাউকে এ অক্ষর সম্বলিত কোনো নাম বা ঠিকানা দেওয়া-নেওয়া করলে বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য ‘জি ফর জেব্রা’ বলা উচিত বলে মনে করেন অনেকে।
মত পার্থক্য কতপ্রকার এবং কি কি তা বৃটিশ আর আমেকিানদের কাছ থেকে যেনো জগৎবাসী শিখে! বৃটিশরা যা করবে আমেরিকানদের যেনো করতে হবে তার উল্টোটা। যেমন, বৃটিশরা গাড়ি বাঁ দিক ধরে চালায় তাই আমেরিকানদের চালাতে হবে ডান দিকে। একসময় কানাডিয়ানরাও বাঁ দিকে চালাতো; আমেরিকানদের সাথে দোস্তি করতে গিয়ে তারাও ডানপন্থী হয়ে গেছে।
মজার আরেকটা বিষয় কেউ লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না- বৃটেনে দূরত্বের হিসেব হয় মাইলে। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এয়ারপোর্ট থেকে তোমার বাড়ি কত দূর সে বলবে ২৫ মাইল অথবা ৩০ মাইল। আর কানাডিয়ান কাউকে যদি একই প্রশ্ন করা হয় বলবে ২৫ মিনিট অথবা ৩০ মিনিট। কানাডিয়ানরা দূরত্ব মাপে সময় দিয়ে। সময়ের মূল্য পৃথিবীতে কানাডিয়ানরা যেভাবে বুঝে বাকি বিশ্ব সেভাবে বুঝে কি?
বাথরুমকে উত্তর আমেরিকায় বলা হয় ওয়াশরুম। ড্রইংরুমকে বলা হয় লিভিংরুম। লন্ডনে যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন এখানে সেটা সাবওয়ে। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়।
কানাডায় আমি যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হই, তখনকার একটি ঘটনা। ক্লাস চলছিল। কাঠপেন্সিল দিয়ে লিখতে গিয়ে ভুল করায়, পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম- “তোমার কাছে কি রাবার আছে?” আমার কথা শুনেই সে মেয়েটি “হোয়াট!” বলে এত জোরে চিৎকার করে উঠলো যে, পুরো ক্লাসের শিক্ষার্থীদের চোখ যেন তীরের মতো আমার দিকে ছুটে এলো। এক অস্বস্তিকর মুহূর্তে পাশে বসা এক গ্রিক সহপাঠিনী এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দিলো। পরে জানতে পারলাম- উত্তর আমেরিকায় ‘রাবার’ বলতে ‘কনডম’ বুঝায়!
এবারে যে শব্দ দুটোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তা হলো ‘ডিনার’ এবং ‘সাপার’।
ডিনার একটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ উপবাস ভঙ্গ করা। সাপার শব্দটি ফরাসি। ১২ শতকে এটাকে ইংরেজি অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর অর্থ, দিনের শেষ খাবার। এবার দেখা যাক কোথায় কীভাবে শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। (অভিধান এবং বাস্তবতা এখানে পরস্পরবিরোধী।)।
ডিনার বলতে উত্তর আমেরিকায় যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে যে খাবার পরিবেশন করা হয় তা হলো ডিনার। ক্রিসমাস, থ্যাঙ্কস গিভিং ডে’র মতো বিশেষ উপলক্ষে ডিনার পরিবেশন করা হয়, যেখানে নানা রকম খাবার থাকে।
সাপার হচ্ছে দিনের তিনবারের আহারের মধ্যে সর্বশেষ নিয়মিত আহার। এটা সাধারণত সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।
লাঞ্চ বলতে উত্তর আমেরিকায় যে অর্থ করা হয় তা হচ্ছে অফিস বা স্কুল সময়ে হালকা প্যাকেটকৃত খাবার। ব্রিটেনে দুপুরের খাবার যাই হোক এটাকে তারা লাঞ্চ বলেই আখ্যায়িত করে থাকে।
অন্যদিকে ডিনার রাতের আহার হলেও দিনের মধ্যবর্তী সময়ের আহারকেও এখানে অনেকে ডিনার বলে থাকে। দিনে দুপুরে বড় কোনো পার্টিতে যেখানে ভূড়িভোজ করানো হয় সেটাকে এরা ‘গালা ডিনার’ বলে প্রচার করতে দেখা যায়।
১৮১৮ সাল থেকে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে একটি ব্যাখ্যা দেয়া আছে। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, একজন মেকানিক দিনে তিনবার আহার গ্রহণ করে। প্রথমটি হলো ব্রেকফাস্ট (এখানে নাস্তা বা জলখাবার কোনোটাই যুৎসই নয়) যা মাছ অথবা মাংসের সঙ্গে কফি থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডিনার যা গরম এবং সমৃদ্ধ খাবার এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সাপার যা সন্ধ্যার সময় চা পানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।
১৯ শতকে ব্রিটেনের জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সেই সঙ্গে তারা তাদের রাতের খাবারের নামকরণ করে ডিনার। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে যে খাবার পরিবেশন করা হবে তা ডিনার নামেই পরিচিত।
সাপার হোক কিংবা ডিনার, নামে কিছু যায় আসে না। কানাডিয়ানরা ঠিকই বোঝে এটা হলো রাতের খাবার। তবে বাঙালি সমাজের জন্য লাঞ্চ হোক কিংবা সাপার অথবা ডিনার যাই বলা হোক সব সমান। আমরা জিজ্ঞেস করি ভাত খেয়েছেন কি?
পুনশ্চ: ইংরেজি অভিধান একটি থাকলেই যথেষ্ট ছিলো যেটা বৃটিশদের অর্থাৎ Oxford English Dictionary। কিন্তু আমেরিকানরা ভাবলো তাদের আলাদা একটা অভিধান চাই। তারা আনলো- Merriam-Webster Dictionary। একই ভাষাভাষীদের দুইভাগে বিভক্ত করে রেখেছে দুই অভিধান।
Oxford English Dictionary যেমন শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে, Merriam-Webster তেমনি টেলিভিশন থেকে টিকটক সবখানে ব্যবহৃত আধুনিক ইংরেজিকে ধরে রাখে।
পুুনশ্চ ২: অভিধানে কিছু থাকুক, বা নাই থাকুক, বাঙালিদের কিছু নিজস্ব ইংরেজি শব্দ আছে।
যেমন দেশে যেটাকে আইসক্রিম বলা হয়, সেটা বাইরের জগতে পপসিকল। আইসক্রিম বলতে ভিন্ন এক জিনিস।
শিক্ষার্থীদের যে ‘লাইব্রেরি’ থেকে বই কিনতে শিক্ষকরা পাঠান সেটা আসলে বুকস্টোর। লাইব্রেরি বলতে সারা বিশ্বের লোক পাঠাগারই বোঝে।
চকলেট বলে যে জিনিসটির সঙ্গে ছোটবেলা থেকে আমাদেও পরিচয়, বিদেশে এসে দেখি এটার নাম ক্যান্ডি। চকলেট হলো পৃথক আরেকটি জিনিস।
পুুনঃপুনশ্চ: ঢাকা থেকে আগরতলা বাস সার্ভিস শুরু হওয়ার পর ভাবলাম ঘুরে আসলে কেমন হয়! যেই ভাবা সেই কাজ! কাউন্টারে টিকিট কাটতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম- আগরতলা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগতে পারে?
কাউন্টার থেকে জবাব এলো- এই ধরেন, সকালে নাস্তা খেয়ে যদি ঢাকা থেকে রওয়ানা দেন তাহলে দুপুরে আগরতলা পৌঁছে ভাত খেতে পারবেন। ভেতো বাঙালি খাওয়া ছাড়া কোনো উদাহরণ দিতে পারে না!