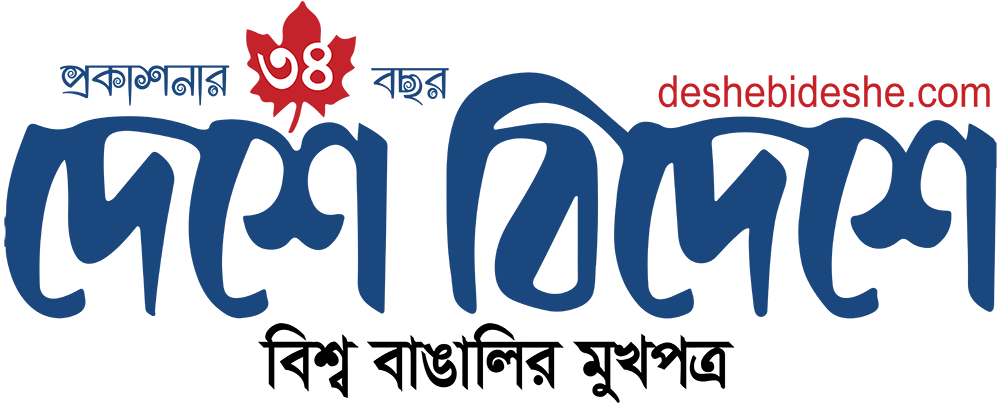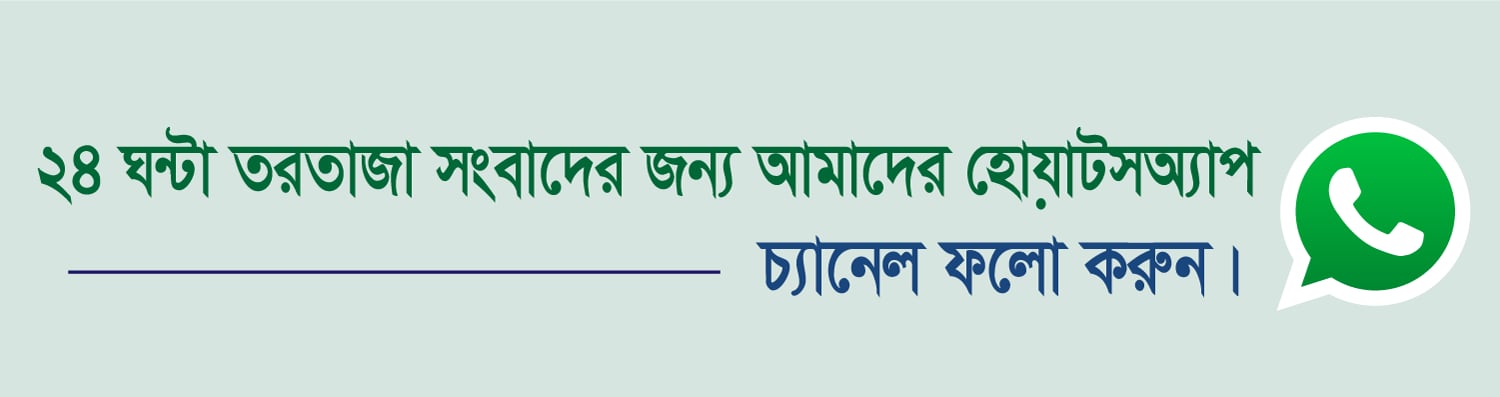নিউ ইয়র্কে প্রথমবার আসা যেন সিনেমার কোনো দৃশ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়া। বিমানের জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখা যায়—লেখার খাতায় আঁকা মানচিত্রের মতো এক শহর, যেখানে আলোই ভাষা, আর ব্যস্ততা যেন ছন্দ। হাডসন নদী শহরের বুক চিরে নীল রেখার মতো চলে গেছে, তার দু’পাশে দালান-কোঠা, পার্ক, সেতু আর রাস্তার জটিল বুনন।
শহরটা বিশাল, কিন্তু কোথাও কোনো শূন্যতা নেই। প্রতিটি কোণে কিছু না কিছু ঘটছে। কেউ ছুটছে কাজে, কেউ হয়তো জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরুতে দাঁড়িয়ে। প্রথমবার নিউ ইয়র্কে পা রাখলে, মানুষের ভিড় আর আকাশচুম্বী ভবনগুলো দেখে মনে হয়—এখানে কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কাউকে খোঁজেও না। অথচ কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে শুরু হয়, এই বিশাল শহরের প্রতিটি পাথরের নিচে লুকিয়ে আছে কোনো না কোনো গল্প।
নিউ ইয়র্কের শুরু হয়েছিল অনেক আগেই—ডাচ উপনিবেশ ‘নিউ আমস্টারডাম’ নামে। পরে ইংরেজরা এসে নাম বদলে দিল ‘নিউ ইয়র্ক’। কিন্তু বদলায়নি শহরের চরিত্র। তখন যেমন মানুষ এসেছিল নতুন সুযোগ খুঁজতে, এখনও প্রতিদিন হাজারো মানুষ আসে—কেউ ভিসা হাতে, কেউ স্বপ্ন বুকে, কেউ কেবল একটি সুযোগের আশায়।
নিউ ইয়র্ক শহর তার নাগরিকদের কোনো নিশ্চয়তা দেয় না, কিন্তু সে দেয় চেষ্টা করার জায়গা। এখানে সবাই ব্যস্ত, সবাই গন্তব্যে—কিন্তু তবুও, কেউ পথ হারালে পথ দেখানোর মতো আলো জ্বলে থাকে ফুটপাতের ধারে, সাবওয়ের সিঁড়িতে, কিংবা কোনো অপরিচিত চোখের হাসিতে।
এ শহর আপন করে নেয় না খুব সহজে, তবে কাউকে ফিরিয়েও দেয় না। কেউ এখানে আসে ক্ষণিকের জন্য, কেউ থেকে যায় সারা জীবন। কিন্তু একবার নিউ ইয়র্কের বাতাসে নিঃশ্বাস ফেললে, এই শহর কিছুটা নিজের হয়ে যায়—চিরদিনের মতো।
নিউ ইয়র্ক শহরে আজ প্রচুর বাঙালির বসবাস। অ্যাস্টোরিয়া, জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিনে হাঁটতে গেলে প্রচুর বাঙালির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাবওয়ে ট্রেন থেকে দেখা যায় বাংলা সাইনবোর্ড। বাংলাদেশের কী নেই নিউ ইয়র্ক শহরে?
বাঙালি মালিকানাধীন শত শত দোকানপাট। চিড়া-মুড়ি থেকে শুরু করে যশোরের খেজুরের গুড়, চট্টগ্রামের শুঁটকি, সিলেটের সাতকরা—সবই আছে। বাংলা পত্রিকা, বাংলা রেডিও, টেলিভিশনও আছে। প্রত্যেক সপ্তাহে দেশের কোনো না কোনো নেতা, শিল্পী, কবি, লেখক অর্থাৎ বিশিষ্ট কেউ না কেউ অবস্থান করছেন। সংগঠনের সংখ্যা বে-শুমার। একটার পর একটা অনুষ্ঠান লেগে আছে।
যে জিনিসটি চোখে লাগে তা হলো, অন্যান্য দেশে বসবাসকারী বাঙালিদের চেয়ে নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী বাঙালিরা ব্যস্ত বেশি। হাঁটার স্টাইল ভিন্নরকম। এ ভিন্নতা লিখে বোঝানো যাবে না, এটা দেখে বোঝার বিষয়।
বিদেশে বাঙালিদের চেনার কয়েকটি উপায় আছে। সাধারণ বাঙালিকে দেখলেই আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যে বাঙালিদের গলায় একটা মাফলার দেখা যাবে। মাফলারওয়ালা বলতেই বাঙালি। ইংল্যান্ডে টাই ছাড়া থ্রি-পিস স্যুট পরা যাদেরকে দেখবেন নিশ্চিত থাকবেন তারা বাঙালি। আমেরিকা-কানাডায় বাঙালি তরুণদের গায়ে দেখা যায় চামড়ার জ্যাকেট। চুলের ছাঁট যেমনই হোক না কেন, গায়ের রং যাই হোক না কেন, না চেনার কোনো কারণ নেই।
বিদেশে বসবাসকারী বয়স্ক বাঙালিদেরও চিনতে কোনো অসুবিধা হয় না, তা ৩০ বছর ধরে থাকুন আর চল্লিশ বছর। তাদের মুখে দেখবেন বিষণ্নতার একটি ছাপ। ‘চিন্তার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়’। হাসিখুশি বয়স্ক বাঙালি লোকের দেখা কদাচিৎ পাওয়া যায়।
গত সপ্তাহে এক ঝটিকা সফরে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলাম। বেশ ক’দিন ধরে যাবো যাবো করছি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। আসলে সুযোগই হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত একদিন আগে টিকিটের বুকিং দিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্রাজিলিয়ান এয়ারলাইন্সে চড়ে বসি। মাসখানেক ধরে পরিচিতজনদের মাধ্যমে বার্তা জানালেও যাওয়ার তারিখ জানানো হয়নি। সে কথা মনে হলো টরন্টো এয়ারপোর্টে গিয়ে। আমার ভাই টিপুকে বললাম আজমকে ফোন করে দিতে।
আজম। পুরো নাম কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম। আত্মীয় না হয়েও যে আত্মীয়। তাকে আমি ছোট ভাইয়ের মতো দেখি। সেও আমাকে নিজের বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করে। তার সঙ্গে আমার পরিচয় আরব আমিরাতে। দুবাই হামরিয়া মার্কেটে তার খুবই ভালো ব্যবসা ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকার বেচাকেনা। একবার আমার প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে এসে তার জীবনের গতিধারা পাল্টে যায়। আমার সঙ্গে শোবিজনেসে চলে আসে। যখন কানাডা আসার সিদ্ধান্ত নিলাম সেও তার ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে তৈরি হয়ে যায়।
এখানে এসে কানাডা ইমিগ্রেশনের ধারাপাত না পড়ে সে তার পাসপোর্ট-টিকিট লুকিয়ে ফেলে। ফলে যা হবার নয় একে একে তাই হতে লাগল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হতে হলো আজমকে। মামলা খারিজ হলো। উকিলের পেছনে হাজার হাজার ডলার খরচ করেও সে আর থাকতে পারল না। তাকে আমেরিকাতে ডিপোর্ট করে দেওয়া হলো। সেই থেকে সে ওখানে আছে।
মানুষের প্রতিভাকে যেমন চাপা দিয়ে রাখা যায় না, তেমনি বুদ্ধি থাকলে মরুভূমি হোক, আর গভীর অরণ্য হোক, সে একটা উপায় বের করবেই। নিউ ইয়র্কের মতো শহরে যেখানে হাজার হাজার ইমিগ্রান্ট রেস্টুরেন্ট আর ইয়েলো ক্যাবের পেছনে ছুটছেন, সেখানে আজম খুলে বসেছে একটি সুপার মার্কেট। জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা নিয়ে গেল ব্রুকলিনে অবস্থিত তার কে অ্যান্ড এস মিনি সুপার মার্কেটে। বিশাল ব্যাপার-স্যাপার। ফ্রিজ খুলে একটা আইসক্রিম নিলাম। খেতে খেতে দেখতে থাকলাম ক্রেতাদের আনাগোনা। জমজমাট কাজ-কর্ম।
আমেরিকা গিয়ে আজম প্রথমে যে গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি করে তা হলো—বিয়ে করা। মেয়েটির নাম বিউটি। সে উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকায় এসেছিল। আজম তার পিছু নেয় এবং শেষপর্যন্ত হৃদয়-মন জয় করে শুভকাজ সম্পন্ন করতে মোটেই বিলম্ব করেনি। খুবই মায়াবি চেহারার ফুটফুটে একটি মেয়েসহ এখন তিনজনের ছোট্ট সংসার তাদের।
রাতের খাবার খেয়ে চলে গেলাম ব্রুকলিনের বাঙালি পাড়ায়। রাত তখন প্রায় দশটা। নিউ ইয়র্কে সেদিন শীতও ছিল খুব। আমরা একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। দেখি বেশ ক’জন আড্ডা দিচ্ছেন। গিয়ে বসলাম তাদেরই পাশের টেবিলে। উত্তপ্ত আলোচনা। বিষয় খালেদা-হাসিনা। কে কী ভুল করছেন, কী করা উচিত, কী উচিত নয় ইত্যাদি। বেশ উপভোগই করলাম তাদের আলাপচারিতা।
ফেরার পথে আজমকে জিজ্ঞেস করলে সে জানালো, রোজই এরা এখানে আসেন। দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম পর্ব রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত চলে, তারপর ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে এরকম একটা পাকিস্তানি রেস্টুরেন্টে আরও ঘণ্টা দুয়েক ফাইনাল আড্ডা দিয়ে তবে তারা ঘরে ফেরে।
আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এদের পরিবার-পরিজন কী এখানে না দেশে? আজম জানালো এখানেই। ঘরে গিয়ে যখন একই বিষয়ে আলাপ করছি, তখন আজমের স্ত্রী বিউটি বললো, “ভাই, কার কাছে কী জিজ্ঞেস করছেন, সেও তো ঐ আড্ডা কমিটির সদস্য।” বিউটি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালো, “পড়াশোনার কথা না হয় বাদই দিলাম, এসব লোকেরা যদি ঘরে এসে টিভি দেখতো, তবুও দুনিয়া সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের বৃদ্ধি পেতো। সংসার-ছেলে-মেয়ের চাইতে যেসব লোকের কাছে আড্ডাবাজি পছন্দ, তারা কী করে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে সেটাই প্রশ্ন।”
সৈয়দ মামুন। একই উপজেলায় আমাদের বাড়ি। ‘দেশে-বিদেশে’ পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে জড়িত। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা অনেকেই দেখে থাকবেন হয়তো। দেশে থাকতেও তিনি শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। মামুন প্রায় ১৫-১৬ বছর ধরে আমেরিকায়। রাতে ফোনে আলাপ হলো। জানতে পারলাম পরদিন তার কাজ আছে। কিছুক্ষণ পর জানালেন তিনি ছুটি নিয়ে নিয়েছেন এবং সকালে এসে আমাকে নিয়ে বেরোবেন।
খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম, মামুনকে একটা সারপ্রাইজ দিই। সাবওয়েতে করে সোজা চলে গেলাম জ্যাকসন হাইটস। সেখান থেকে এন ট্রেনে ৪০ স্ট্রিটে তার বাসায়। নাশতা সেরে আমরা বের হয়ে পড়লাম। বাংলাদেশ কনস্যুলেট, সোনালী এক্সচেঞ্জ, বিমান অফিস ঘুরে গেলাম সাপ্তাহিক ‘প্রবাসী’র দপ্তরে। সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম ‘সাপ্তাহিক ঠিকানা’র দপ্তরে।
সন্ধ্যায় ফকির ইলিয়াস আয়োজন করেছিলেন এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানের। বাঙালি মালিকানাধীন একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ঐ অনুষ্ঠানে দেখা হলো রূপসী বাংলা টিভি অনুষ্ঠানের পরিচালক আনিসুজ্জামান খোকন, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রবাসীর শিকদার হুমায়ূন কবীরসহ আরও অনেকের সঙ্গে। নৈশভোজ শেষে ঘরে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল।
ব্যস্ত নগরী নিউ ইয়র্ক। যেসব বিষয় চোখে লাগলো তার মধ্যে যা উল্লেখ না করলেই নয়, তা হলো—বাঙালি সবাই কাজ করছেন। বৈধ-অবৈধ বলে কথা নেই, সকলেই কাজ করে খাচ্ছেন। কাজ শেষে প্রথম নেশা হলো সংগঠন করা এবং সেই সঙ্গে পত্রিকা পড়া। ফেরার দিন আজমকে বললাম, “খুব দুঃখ নিয়ে টরন্টো ফিরে যাচ্ছি।”
সে ঘাবড়ে জিজ্ঞেস করল, “কেন? কী দুঃখ পেলেন?” বললাম, “এ পর্যন্ত কোনো সাধারণ লোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো না। যতজনের সঙ্গে তুমি পরিচয় করিয়ে দিলে, তারা সকলেই কোনো না কোনো সংগঠনের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক।”
আজম বললো, “তাহলে এটাও জেনে নেন যে, নিউ ইয়র্কের ৯৯ শতাংশ লোকের নাম কোনো না কোনোভাবে পত্রিকার পাতায় এসেছে।” বললাম, “যে এক শতাংশের নাম আসেনি, তা নিতান্তই ভুলে বাকি রয়ে গেছে—তাই না?” আজম হাসতে লাগল।
আরেকটা বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো—বিভিন্ন এলাকায় নজর কাড়া বাংলা সাইনবোর্ড। এই একটি কাজের জন্য নিউ ইয়র্কের বাঙালিরা আর কিছু না করলেও যুগ যুগ ধরে গোটা জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র, আর সে দেশের প্রধান শহর নিউ ইয়র্কে শত শত বাংলা সাইনবোর্ড ঝুলছে—এ চাট্টিখানি কথা নয়!
দেখলাম, বাঙালি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টগুলো খুব চলছে। বাঙালিরাই খাচ্ছে। দুপুরের খাবার, রাতের খাবার নাকি অনেকেই হোটেলেই সারেন। ‘আলাদীনস’ বা ‘আলাউদ্দিন’ নামের রেস্টুরেন্ট আছে বেশ কটি।
গ্রোসারিগুলোও চলছে খুব। বাংলাদেশের কী কী পাওয়া যায় তা উল্লেখ না করে বলবো—কী কী পাওয়া যায় না, তার তালিকা করা সহজতর হবে। ভিডিওর দোকান আছে বেশ কিছু। বাংলাদেশের ছায়াছবি আর নাটকে ঠাসা। রয়েছে বাংলা অডিও ক্যাসেট, সিডি—কত কী!
নিউ ইয়র্কে বাংলা বইয়ের দোকানও রয়েছে। একটার নাম ‘মুক্তধারা’, অন্যটি ‘অনন্যা’। মুক্তধারার বিরাট সংগ্রহ। রামায়ণ থেকে আল কোরআন, রবীন্দ্রনাথ থেকে হুমায়ূন আহমেদ—সবই আছে।
হাজার বলবো না, লক্ষ বলবো বুঝতে পারছি না। তবে বাংলাদেশের যে কোনো বড় বুকস্টোর থেকে কোনো অংশে কম নয়। সারাক্ষণ ভিড় লেগেই আছে। ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে হয়। আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে ক্রেতারা আসেন বই কিনতে।
আমেরিকা প্রবাসীদের এ এক সৌভাগ্য বলা যায়। দেশে যা পাওয়া যাচ্ছে না, এখানে তাও পাওয়া যাচ্ছে। শুধু কী বই? অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিনের বিরাট সমাহার।
মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহা জানালেন, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে তাদের গ্রাহক রয়েছেন। অগ্রিম টাকা পাঠালে তারা ডাকযোগে বই পাঠান। অতি উত্তম ব্যবস্থা। ব্যবসা দেখে বিশ্বজিৎকে বললাম, “আপনি তো এ বছরেই মিলিওনিয়ারদের খাতায় নাম লেখাবেন দেখছি।” অমায়িক একটা হাসি দিয়ে তিনি বললেন, “এটা আপনাদের সকলের আশীর্বাদ। গত আট বছর বহু কষ্ট করেছি। নিজের বাড়ি থেকে বইয়ের ব্যবসা শুরু করে আজ এ পর্যন্ত এলাম। দেখা যাক কী হয়।”
তাঁর কাছে জানলাম, দুই বাংলার কবি, লেখক, সাহিত্যিক যতজনই নিউ ইয়র্ক এসেছেন, মুক্তধারাতে একবার সকলেই পদধূলি দিয়েছেন। সপ্তাহখানেক আগে বাংলাদেশের স্বনামধন্য লেখক হুমায়ূন আহমেদও এসেছিলেন। তিনি মুক্তধারার সঙ্গে একটি চুক্তিনামায় সই করে গিয়েছেন। চুক্তি হলো—হুমায়ূন আহমেদের যেসব বই বাংলাদেশে প্রকাশিত হবে, তা ঢাকার বাজারে দেওয়ার আগেই মুক্তধারাকে দেবেন। এমনকি ‘নূহাশ চলচ্চিত্র’-এর ব্যানারে যেসব নাটক এবং চলচ্চিত্র হবে, সেগুলোও বাংলাদেশের দর্শকরা দেখার আগেই মুক্তধারা পাবে। বিশ্বজিৎ বিরাট কাজ করে ফেলেছেন। এটাও আমেরিকা প্রবাসীদের সৌভাগ্য বলতে হয়। তারা সবার আগে পড়বেন, সবার আগে দেখবেন।
নিউ ইয়র্কে ফোনকার্ডের ব্যবসা বেশ জমজমাট। প্রায় ঘরে দেখলাম, তারা লং ডিস্ট্যান্স কেটে দিয়েছেন। যখনই তাদের লং ডিস্ট্যান্স ফোন করতে ইচ্ছে হয়, তারা কার্ড ব্যবহার করেন। এটা নাকি তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা।
টরন্টো, মনট্রিয়ল-এর সঙ্গে নিউ ইয়র্কের পার্থক্য অনেক কিছুতে। একটি পার্থক্য খুব বেশি চোখে লেগেছে, যা না বলে পারছি না, আর তা হলো—টরন্টোর রাস্তায় কোনো গাড়ি ডানে, বামে কিংবা সামনে যেতে চাইলে অন্যজন তাকে সসম্মানে এগুতে দেয়। কিন্তু নিউ ইয়র্কে সে সৌজন্যতা কেউ দেখায় না।
বাঙালি অনেকের গাড়িতে ‘ডান্ডবেড়ি’ দেখলাম। গাড়ি চুরি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্টিয়ারিংয়ে লোহার রডের তালা। বাঙালিরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করে চলেন।
নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা এখন ছয়। মাসিক, ত্রৈমাসিক বিভিন্ন সংকলনের কোনো হিসাব নেই। আরও কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। সাংবাদিকের সংখ্যা অগণিত। যে কজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সকলেই পেশাদার সাংবাদিক। দেশে পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাদের সঙ্গে আলাপ হলো এবং অবশেষে ঘোষণা দিলাম—অচিরেই সাপ্তাহিক ‘দেশে-বিদেশে’র নিউ ইয়র্ক সংস্করণ বেরোতে যাচ্ছে।
নিউ ইয়র্ক, ১৭ মার্চ ১৯৯৮