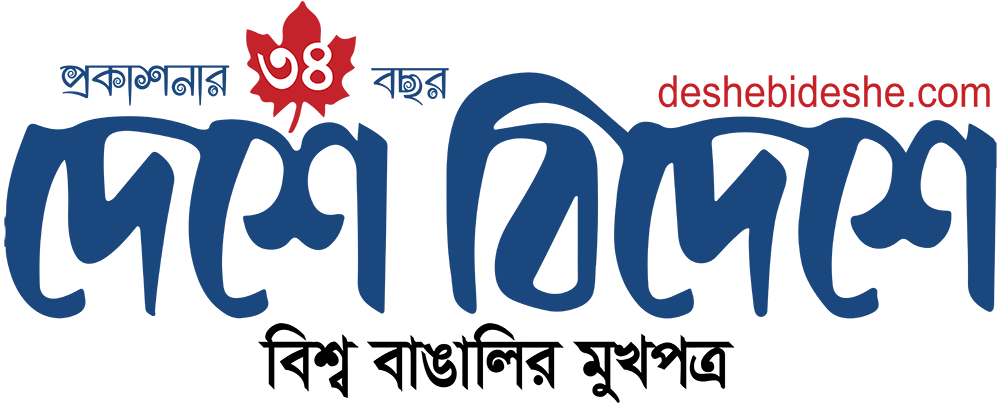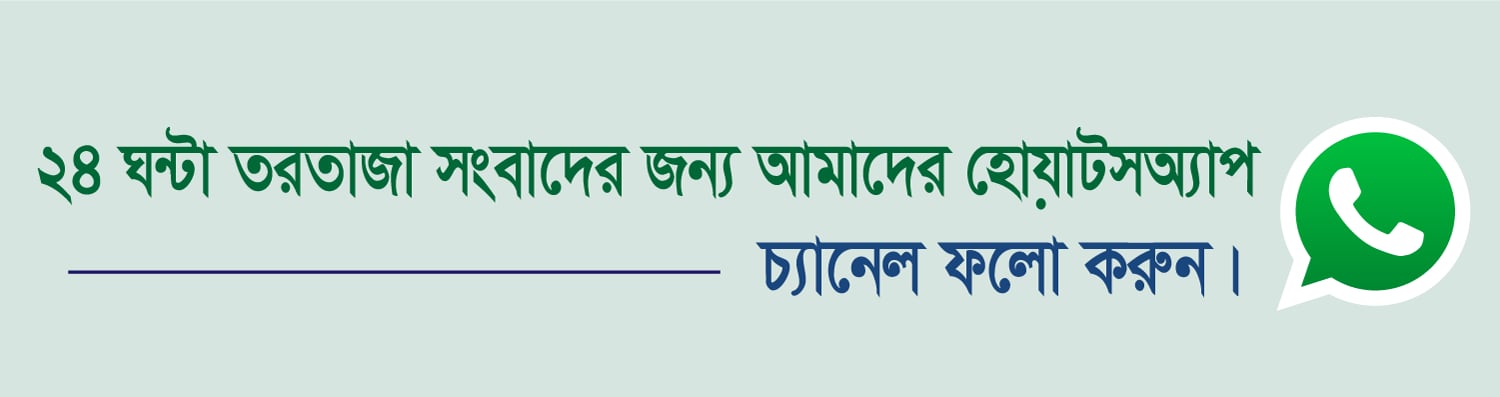হায়দ্রাবাদ, ২৩ জুলাই – ১৪ই ডিসেম্বর সকাল। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সারা ঢাকা শহরে কারফিউ। শান্তিবাগের বাসায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাত বছর বয়সী ছেলে সুমনকে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী দেখছেন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বিমানগুলো নিচু হয়ে উড়ে গিয়ে কাছেই কোথাও বোমা ফেলছে। পাশে দাঁড়ানো ছেলের এক হাত চেপে তিনি হাস্যমুখে বললেন, ‘দেখেছো বাবা, যুদ্ধ বিমানগুলো কতো নিচ দিয়ে উড়ে গিয়ে বোমা ফেলছে। আমাদের বিজয় খুব নিকটেই। এক দুদিনের মধ্যেই আমরা স্বাধীন হব।’
বলতে বলতেই তিনি দেখলেন সাঁই করে আরও দুটো বিমান উড়ে গেল পুরান ঢাকার দিকে। এবার শিশুর মতো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি বললেন, ‘আমাদের বিজয় কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরাই জয়ী হব। কত কাঙ্ক্ষিত বিজয় আমাদের!’
এরই মধ্যে দুপুরের ভাত দেওয়া হয়েছে ডাইনিং টেবিলে। তার স্ত্রী সৈয়দা তাহমিনা মনোয়ারা নুরুন্নাহার বারবার তাগাদা দিচ্ছেন, ‘গোসলটা করে ফেল। কয়টা বাজে খেয়াল আছে? টেবিলে ভাত দিয়েছি।’
স্ত্রীর তাগাদায় বাথরুমে গোসল করতে ঢুকবেন ঠিক এমন সময়ই দরজায় ঠক-ঠক।
তার ভাই লুৎফুল হায়দার চৌধুরী শুনেই ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে ড্রয়িং রুমের পাশ দিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা খুললেন। দেখলেন পাঁচ-ছয় জন মুখোশধারী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
লুৎফুল হায়দার চৌধুরী দরজা খুলতেই মুখোশধারীরা ইংরেজিতে তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘প্রফেসর মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কোথায়? স্যার কি বাসায় আছেন?’
লুৎফুল হায়দার চৌধুরী বললেন, ‘কেন? তাকে কি প্রয়োজন?’
জবাবে মুখোশধারীদের মধ্যে একজন বললেন, ‘তার সঙ্গে আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব জরুরি কথা বলবেন। সে জন্যই আমরা তাকে নিতে এসেছি।’
লুৎফুল হায়দার চৌধুরী বললেন, ‘এভাবে তো নিয়ে যেতে পারেন না আপনারা। আপনাদের কাছে কি কোন ওয়ারেন্ট আছে?’
জবাবে মুখোশধারীরা কিছু না বলেই ঘরে ঢোকার চেষ্টা করল। এমন সময় পথ আগলে দাঁড়ালেন লুৎফুল হায়দার চৌধুরী। মুখোশধারীরা বলল, ‘দেখি সরে দাঁড়ান। আমরা ঘরে ঢুকব।’
কিন্তু, লুৎফুল হায়দার চৌধুরী এক ইঞ্চিও পিছু সরলেন না। এমন সময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আমিই মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বলুন কি বলবেন?’
‘আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে,’ বলল মুখোশধারীরা।
‘কেন কি প্রয়োজন?’
‘ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে। কিছু কথা আছে আপনার সাথে। কথা শেষ হওয়ার পর আমরাই আপনাকে দিয়ে যাব,’ বলল এক মুখোশধারী।
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বললেন, ‘আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি কাপড় পাল্টে নিচ্ছি।’
কিন্তু মুখোশধারীরা বলল, ‘কিছুক্ষণের মধ্যেই তো চলে আসবেন। কাপড় পরিবর্তন করতে হবে না।’
তবুও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কাপড় পাল্টাতে চাইলে তারা বলল, ‘আচ্ছা আপনি আমাদের সামনেই কাপড় পরিবর্তন করে আমাদের সঙ্গে চলেন।’
তিনি কাপড় পরিবর্তন করা মাত্রই মুখোশধারীরা তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর স্ত্রী তাহমিনা এই অবস্থা দেখে বললেন, ‘উনি এখনও কিছু খাননি। গোসল অব্দি করেননি। আপনারা উনাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?’
এক মুখোশধারী জবাব দিলো, ‘ভাবি, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়েই স্যারকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। উনি তো আমাদের শিক্ষক। তার কোন ক্ষতি তো আমরা করতে পারি না।’
কিন্তু, তার কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না তাহমিনা। তার কান্নাজড়িত কণ্ঠ বাঁধ মানল না। দেখেই মৃদু হেসে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বললেন, ‘তোমরা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। আর আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। আমি আবার তোমাদের মাঝেই ফিরে আসব।’
তাকে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছিল, তখন তার ভাই লুৎফুল হায়দার চৌধুরী বললেন, ‘আপনারা আমার ভাইকে নিয়ে যাচ্ছেন। একটু খেয়াল রাখবেন।’
এক পর্যায়ে তিনি মুখোশ পরা একজনকে বললেন, ‘আচ্ছা আপনি মুখোশ পরে আছেন কেন?’ এই বলে তিনি ওই লোকটির মুখে বাধা রুমালটি সরিয়ে ফেললেন।
তখন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাকে ধরে রাখা ছেলেটিকে দেখেই চিনতে পেরে বললেন, ‘তুমি মাঈনুদ্দিন না?’
ছেলেটি উত্তরে বলল, ‘জ্বি স্যার, আমি মাঈনুদ্দিন। আপনার ছাত্র।’
তাহমিনা ও লুৎফুল হায়দার চৌধুরী নিচে নেমে দেখলেন বাসার নিচে একটা কাদা মাখা মাইক্রোবাস আর পাকিস্তানী হানাদারদের গাড়ি। সঙ্গে প্রায় কুড়ি জনের মতো সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে।
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে সেই কাদামাখা মাইক্রোবাসে ওঠানো হলো। তখন স্ত্রী তাহমিনা ও তার ভাই বললেন, ‘আপনারা উনাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, আমরাও সেখানে যাবো।’
কিন্তু, সে কথায় পাত্তা না দিয়ে মাইক্রোবাস চলল অজানার উদ্দেশ্যে। তাহমিনা ও লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর পায়ের নিচের মাটি যেন সরে গেছে। লুটিয়ে পড়লেন তাহমিনা।
না। এরপর আর ফিরে আসেননি। ফিরে আসেননি অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে তাকে এভাবেই দিনে দুপুরে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় একাত্তরের নরপিশাচ চৌধুরী মাঈনুদ্দিনের নেতৃত্বে আলবদর ও হানাদারদের একটি দল।
তাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে। সেখানে আগেই তুলে আনা হয়েছিল অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীসহ অনেক অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ও সাংবাদিকদের।
এসময় তাদের ওপর চালানো হয়েছিলো ভয়ংকর নিষ্ঠুর নির্যাতন। সেই টর্চার সেল থেকে ফিরে আসতে পেরেছিলেন কেবল দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেছিলেন কেমন ছিল সেদিনের ঘটনা।
‘রাত তখন সাড়ে আটটার কাছাকাছি। লোহার রড হাতে অন্ধকার ঘরটাতে পা রেখেছিল কিছু যুবক। প্রথমে তারা মুনীর চৌধুরীর মুখোমুখি হয়েছিল। বলছিল, “ছাত্রদের তো অনেক কিছু শিখিয়েছেন। আজ আমরা আপনাকে কিছু শিক্ষা দেব।” তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আপনি কয়টা বই লিখেছেন?” মুনীর চৌধুরী দুদিকে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, “তিনি লেখেননি।” মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কাছেও ছিল তাদের একই প্রশ্ন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেছিলেন, “হ্যাঁ, আমি লিখেছি।” এ কথা শুনেই রড দিয়ে তার ওপর চালানো হয়েছিল পৈশাচিক নির্যাতন।’
সেদিন যাদের ধরে আনা হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মোহাম্মদপুরের কাটাসুরে। তারপর তার ভাগ্যে কি হয়েছিলো কেউ জানে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই কিংবদন্তী বুদ্ধিজীবীর মরদেহটি শেষমেশ খুঁজেও পাওয়া যায়নি।
কিংবদন্তী গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জন্ম ১৯২৬ সালের ২২ জুলাই নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার খালিশপুর গ্রামে। তার বাবা বজলুর রহমান চৌধুরী সেকালেই ছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তার মা মাহফুজা খাতুন তেমন একটা পড়াশোনা না করলেও, দারুণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র নয় বছর বয়সেই বাবাকে হারিয়েছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল মা ও মামার আশ্রয়ে।
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল নোয়াখালীতে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। এরপর নোয়াখালী আহমদিয়া ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পূর্ববঙ্গ থেকে প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ হয়েছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। দুই বছর পরে ১৯৪৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে তিনি সমগ্র ঢাকা বোর্ডে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।
এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। কিন্তু, সেখানে তার ভাল না লাগায় বাংলা বিভাগে পরিবর্তিত হয়ে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। তখন শান্তিনিকেতনের সিলেবাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায়।
এ সময় তাদের বাড়িতে সম্পত্তি নিয়ে বেশ টানাপোড়েন চলছিল। তার মা একাই সব সামলাচ্ছিলেন। এমন সময় দাঙ্গা শুরু হলো ভারতবর্ষে। বাধ্য হয়ে গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীতে চলে গেলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। বাড়ি এসে দেখলেন পারিবারিক সেই বিরোধ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। শেষে বহু কষ্টে তিনি সেই পারিবারিক বিরোধ মেটালেন। যদিও এর জন্য তাঁদের বহু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়েছিল।
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী যে বছর স্নাতকের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, সে বছর ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০তম বর্ষ। আর সেই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের ইতিহাসের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।
সর্বকালের সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় তাকে সে বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘সুরেন্দ্রনলিনী স্বর্ণপদক’ প্রদান করে। দেশভাগের আগেই ১৯৪৭ এর জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনের বৃত্তি পেয়ে সেখানে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। এর মধ্যে দেশ থেকে কয়েক মাস পর ফিরে গিয়ে ১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। তার এই গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ‘সাহিত্যভারতী’ সম্মাননা দিয়েছিল।
এ সময় তিনি চাইলে ভারতে নির্দ্বিধায় থেকে যেতে পারতেন। কারণ, একই সঙ্গে সেখানে তাঁর গবেষণার দারুণ সুযোগ এবং ভালো চাকরির প্রস্তাব ছিল। কিন্তু, তিনি নিজের মাতৃভূমিকে ছেড়ে থাকতে পারেননি। আর তাই ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শান্তিনিকেতন ছেড়ে ঢাকায় চলে এলেন।
ঢাকায় এসে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী পাণ্ডুলিপি রচয়িতা হিসেবে যোগ দিলেন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে। পরের বছর জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবেও শিক্ষকতা শুরু করেন। একই সময়ে সেন্ট গ্রেগরিজ কলেজেও (বর্তমানে নটরডেম কলেজ নামে পরিচিত) খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করতেন তিনি। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, শিক্ষকতাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়তেন তিনি।
এত ব্যস্ততার পরেও এই অসামান্য মেধাবী ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় হয়েছিলেন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। দুই বছর পর ১৯৫৫ সালে লেকচারার হিসেবে যোগ দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই।
১৯৫৬ সালে সৈয়দা তাহমিনা মনোয়ারা নুরুন্নাহারের সঙ্গে বিয়ে হয় মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর।
১৯৫৭ সালে তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ভাষাবিজ্ঞানে পড়ার জন্য বৃত্তি পান তিনি। সেখানে দুই বছর গবেষণা করার পর তিনি কথ্য বাংলার শব্দের ছন্দবিজ্ঞানের ওপর একটি থিসিস পেপার লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তার গবেষণার ধরন তৎকালীন মার্কিন ধারার ভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণাপন্থার অতিমাত্রায় অনুসারী ছিল বলে এই থিসিস পেপার আর প্রকাশিত হয়নি। স্বাধীনতার পরে সেটি ‘Some Supra-Segmental Phonological Features of Bengali’ নামে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।
১৯৬৪ সালে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাবিজ্ঞান পড়ার উদ্দেশে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত সেবার তিনি যেতে পারেননি। পরে ১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে তাকে সংবর্ধনা দিয়েছিল।
একাধারে গবেষক ও ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন কিংবদন্তীতুল্য। মননশীল প্রবন্ধেও তিনি ছিলেন ভীষণ উঁচু মানের প্রাবন্ধিক। বিশেষ করে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তার লেখা বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার ছিলো বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক কাজ। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত তার লেখা রবি পরিক্রমা, রঙিন আখর ছিল অসামান্য দুই গ্রন্থ।
১৯৬৯ সালে প্রকাশিত তার লেখা প্রবন্ধ সংকলন ‘সাহিত্যের নব রূপায়ণ’ ছিল বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শিক্ষাজীবনে যেমন ছিলেন দুর্দান্ত ও তুখোড় মেধাবী এবং ভীষণ প্রতিভাবান, তেমনি শিক্ষকতা জীবনেও তার মতো শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে খুব কমই এসেছে। শিক্ষার্থীদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন তিনি। তাদের সঙ্গে তিনি ছিলেন বন্ধুর মতো। সদা হাস্যোজ্জ্বল, অনন্য ব্যক্তিত্ববান ও ক্ষুরধার সরল এই মেধাবী গবেষক শিক্ষককে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল কেবল তার বিচার বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিশ্বাসের জন্য।
চিন্তা ও চেতনায় তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। পঞ্চাশের দশকে তমদ্দুন মজলিশে পূর্ব বঙ্গের বাংলা সাহিত্যে অমুসলিম সাহিত্যিকদের কোনো সাহিত্যকর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না বলা হলে তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ করে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথকে মুছের ফেলার ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালে যখন রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হলে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।
মুক্তিযুদ্ধে তিনি যেমন পরোক্ষভাবে নানা সহযোগিতা করেছিলেন মুক্তিবাহিনীকে। ঠিক তেমনি নিয়মিত ক্লাস করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়েও। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে কিছুদিনের জন্য ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা। কিন্তু, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী যাননি। ছাড়েননি নিজের মাতৃভূমি।
তিনি বলতেন, ‘আমার দেশ ছেড়ে আমি যেতে কোথাও যেতে পারি না। মরলে এই দেশেই মরব।’
এটাই যেন নির্মম সত্য হয়ে ঘটল এই কিংবদন্তী শহীদ বুদ্ধিজীবীর জীবনে।
আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষণজন্মা গবেষক, শিক্ষাবিদ ও কিংবদন্তী বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জন্মদিন। জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধায় নত চিত্তে স্মরণ করি এই অনন্য প্রতিভাবান শহীদ বুদ্ধিজীবীকে।
এন এইচ, ২৩ জুলাই