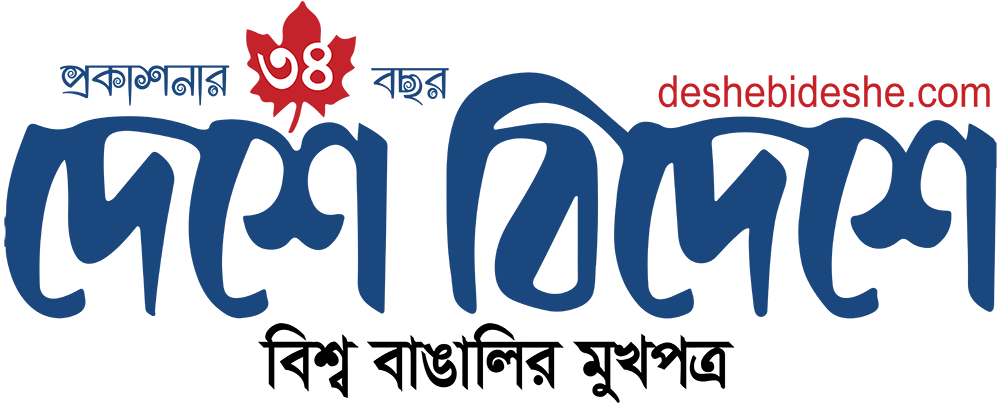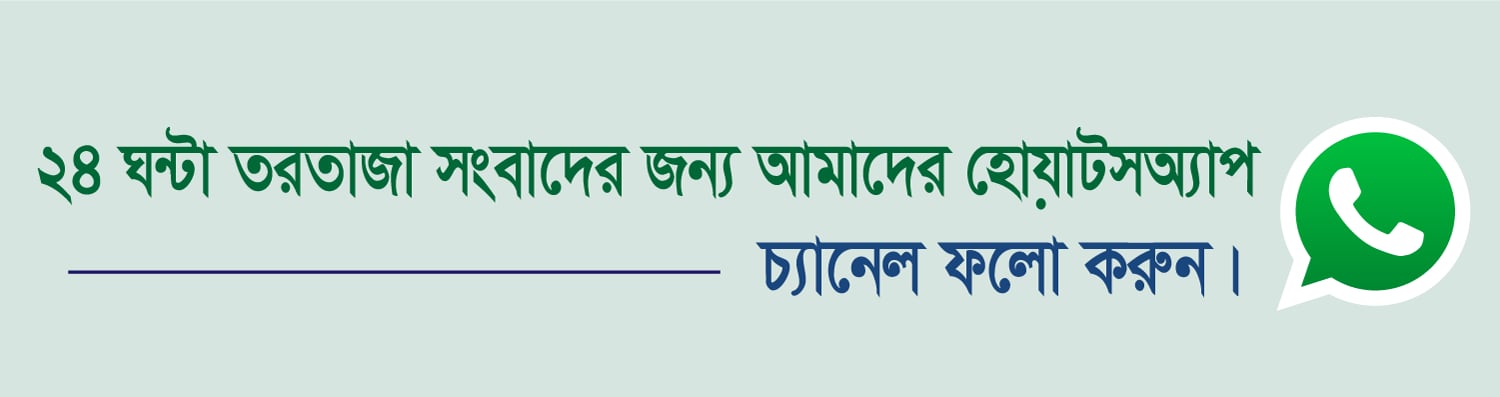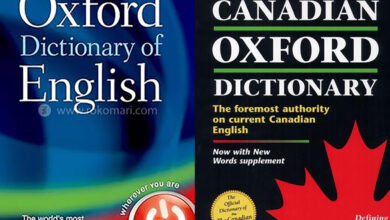বার্মিংহামের আকাশটা ধূসর, মাঝে মাঝে সোনালি আলো এসে মাটির রঙ পাল্টে দেয়। পাতাঝরার দিনে রাস্তাঘাটে লাল-হলুদের মিছিল, আর বসন্তে বৃষ্টি যেনো কেবল ফুল গজানোর ইশারা। এই শহরের বুক চিরে চলে গেছে শতশত রাস্তা—কিছুটা নতুন জীবন খোঁজার পথে, কিছুটা পুরোনো জীবন ভুলে থাকার আশায়।
অ্যালাম রক, স্মল হিথ, অ্যাস্টন—এই এলাকাগুলো যেন এক একটি ক্ষুদ্র বাংলাদেশ। বার্মিংহামে বাংলাদেশি অভিবাসীরা প্রথম পা রাখেন ১৯৬০-এর দশকে। প্রথমে এসেছিলেন টেক্সটাইল কারখানায় কাজ করতে, কেউ বা পাটের ব্যবসায়, কেউ কেউ রেস্টুরেন্টে ডিশওয়াশার হয়ে। এরপর একে একে গড়ে উঠেছে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, মেইন রোডের ধারে ধারে বাংলাদেশি গ্রোসারি দোকান।
এই শহরেরই এক কোণে, পেলহ্যাম রোডের একটি বাড়িতে একদিন নিঃশব্দে নিভে গেল এক জীবন—নাম ছিল তার লিলিমা আক্তার মুন্নি। তার গল্প আজও বার্মিংহামের বাতাসে ভাসে, অপ্রকাশ্য এক দীর্ঘশ্বাস হয়ে।
লিলিমা এসেছিল ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে। শান্ত স্বভাব, বড় চোখ, স্বপ্ন দেখার অভ্যেস ছিল তার। পরিবারের অনেক আশা ছিল, বিদেশে বিয়ে হচ্ছে—ছেলেটি ইংল্যান্ডে থাকে, ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে। ২০০৪ সালে মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার এক গ্রাম থেকে ফিরে এসেছিল বাংলাদেশে। পারিবারিক পছন্দে বিয়ে হলো। ছেলেটি প্রবাসী, ১৯৯৮ সাল থেকে বার্মিংহামে বসবাস করছে, অটোমোবাইল কারখানায় কাজ করে। বিয়ের পরের বছরই তারা ফিরে এল বার্মিংহামে—নতুন ঘর, নতুন জীবন।
কিন্তু নতুনত্ব শুধু শহরের ছিল, জীবনের নয়।
লিয়াকতের চোখে ছিল জমি—বাংলাদেশে স্ত্রীর পরিবারের একটি জমি নিয়ে দীর্ঘ লালসা। শ্বাশুড়ি সেই জমি ছেলের নামে লিখে দিতে অস্বীকৃতি জানাতেই শুরু হলো দাম্পত্যের ভেতরে বিষ ঢালা। প্রথমে হালকা চিৎকার, পরে ধমক, তারপর লাথি-ঘুষি। লিলিমা বুঝতে পারেনি, নতুন দেশে তার ভবিষ্যৎ কেবলই কাঁটা দিয়ে বিছানো।
২০০৮ সালে প্রথম পুলিশ আসে। এক রাতে প্রতিবেশীরা ফোন করেছিল—চিৎকার শুনেছে। পুলিশ এসে দেখে, লিলিমার গাল ফোলা, চোখ লাল। লিয়াকতকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু সে যে আগুন, একটুখানি পানিতে নিভে যায় না।
দুজনের দুটি সন্তান—তানিয়া আর সুমাইয়া। বড়টির বয়স তখন ৮, ছোটটির ৫। তাদের চোখে মা ছিলেন পৃথিবীর আশ্রয়, আর বাবা এক অভ্যস্ত ভয়।
২০১৩ সালের ১৩ জুন, স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। দুই বোন দাঁড়িয়ে ছিলো স্কুল গেটের পাশে—মা আসবে, হাত ধরে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু মা এলো না। সময় গড়িয়ে সন্ধ্যা, তারপর রাত। পরিবারের এক আত্মীয় ফোন করলেন পুলিশে।

১৪ জুন ভোরবেলা, পুলিশ এল সেই ভাড়া করা বাড়িতে। দরজা বন্ধ, বাতি জ্বলছে না, চারপাশ নিস্তব্ধ। দরজা ভেঙে ঢুকে সিঁড়ির নিচে, এক কোণে পড়ে থাকতে দেখা গেল লিলিমার শরীর। গলায় দাগ—বদ্ধ ও অস্থির হাতের ছাপ। ময়নাতদন্ত বলল, সে অনেকক্ষণ ধরে শ্বাসরোধের শিকার হয়েছে।
আর লিয়াকত? সে বাইরে ঘুরছিল। অভিনয় করছিল, “লিলিমা কোথায়? স্কুল থেকে নেয়নি কেন?” সে জানতো, অভিনয়ই এখন তার বাঁচার একমাত্র চেষ্টা।
বিচার শুরু হলো বার্মিংহাম ক্রাউন কোর্টে। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি রবার্ট প্রাইস জানালেন, এটি একটি “ঠান্ডা মাথায় করা হত্যাকাণ্ড”। কোর্ট শুনলো, লিয়াকত বলেছিল, “জমির দলিল আমার নামে না করলে আমি ওকে মেরে ফেলব।” এবং সে বলেছিলো ঠিকই।
বিচারক প্যাট্রিক থমাস বলেন, “তুমি কারো ভিন্নমত মেনে নিতে পারো না, সেটাই তোমার সবচেয়ে বড় অন্ধত্ব। তুমি অনেক আগেই সহিংসতা শুরু করেছিলে। এই হত্যাকাণ্ড তারই এক করুণ পরিণতি।”
রায় এলো—জীবনভর কারাদণ্ড। কমপক্ষে ১৫ বছর থাকতে হবে শিকল পরা বন্দিত্বে।
বার্মিংহামের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নেমে এলো গভীর শোক। সেই সন্ধ্যায় মসজিদের ইমাম বললেন, “লিলিমা আমাদের সমাজের এক প্রতীক। আমরা কতটুকু নিরাপদ করেছি আমাদের নারীদের জন্য? বিদেশে এসেও যদি তারা গৃহে অনিরাপদ থাকে, তাহলে আমাদের সভ্যতা কোথায়?”
এক প্রতিবেশী, যিনি প্রায়ই লিলিমার সঙ্গে বাজার করতেন, বললেন, “মেয়েটা খুব চুপচাপ ছিল। কখনো কারো বদনাম করত না। নিজের কষ্ট নিজের ভেতর রাখত।”
এক আত্মীয় বলেন, “আমরা তো ভেবেছিলাম সে ভালো আছে। কে জানতো, এতটা অসহায় হয়ে গিয়েছিল!”
তাদের ছোট মেয়ে সুমাইয়া আজও রাতে ঘুমাতে পারে না। সে বলে, “আমার মা কই?” বড় মেয়ে তানিয়া এখন ১৩, কিন্তু সে কোনো কথা বলে না—চুপ করে তাকিয়ে থাকে জানালার বাইরে।
মুক্তাগাছার সেই মাটির বাড়ি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। লিলিমার মা সেই জমি আজও নিজের নামে রেখেছেন—কারণ সে জমিতে এখন মেয়ের একটি নামফলক বসেছে, ছোট্ট এক স্মৃতি স্তম্ভ। যেখানে লেখা আছে:
“আমার মাটি, আমার মেয়ে, আমার কান্না—সব একসঙ্গে।”
এখানেই প্রশ্ন উঠে—এই মৃত্যু কি শুধু লিয়াকতের হাতে? নাকি সমাজের? আত্মীয়দের? যারা দেখে নেয়, চুপ থাকে? যারা বলে, “বিয়ে টিকিয়ে রাখো,” যারা বোঝে না, একটি জীবন ভেঙে গেলে তাতে ঘরের নাম থাকে না, কেবলই শূন্যতা জমে।
লিলিমা মারা গেছে। কিন্তু তার গল্প এখনও জীবিত। প্রতিটি অভিবাসী নারীর হৃদয়ে এক লুকানো শ্বাসরোধের মতো। সে চিৎকার করে না, শুধু জানালায় একখণ্ড শাড়ি উড়ে—আলো ছুঁয়ে বলে যায়, “আমি হারিয়ে গেছি, কিন্তু আমার গল্প শুনো।”
লিলিমা আজ আর নেই। তার ছোট মেয়েটি এখনো মাঝরাতে চমকে ওঠে—মা হারানোর সেই অনুভব বুকের মধ্যে যেন একটা স্থায়ী গর্ত হয়ে গেছে। বড় মেয়েটা চুপচাপ, অতীত স্মৃতি আঁকড়ে ধরে এখন কেবল নীরব দৃষ্টি ফেলে স্কুলের মাঠে, জানালার আকাশে। তাদের জীবনের সংজ্ঞা বদলে গেছে—‘মা’ এখন আর ব্যক্তি নয়, শুধু এক ব্যথার প্রতিধ্বনি।
মুক্তাগাছায় লিলিমার মা আজও সেই জমির পাশে হাঁটেন, যেটির জন্য তার মেয়েকে দিতে হয়েছে জীবন। জমির মাপ বদলায়, দলিল বদলায়, কিন্তু বুকের শূন্যতা থেকে যায় স্থায়ী।
কমিউনিটির মানুষজন আজও বলে, “আমরা তো ভেবেছিলাম, বিদেশ মানেই নিরাপদ জীবন।” কিন্তু এই ঘটনার পর বারবার প্রশ্ন ওঠে—আসলে কি আমরা নারীদের সুরক্ষা দিতে পেরেছি? না কি তারা কেবলই স্বপ্ন দেখার অধিকার রাখে, বাস্তবের ঘর তাদের জন্য নয়?
লিয়াকত এখন কারাগারে। তাকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দণ্ড। কিন্তু সেই দণ্ড কি লিলিমাকে ফিরিয়ে দিতে পারে? কিংবা তার সন্তানদের মায়ের ভালোবাসা?
সমাজ একেক সময় ঘাতকের চেয়ে নীরব দর্শককে বড় অপরাধী বানায়। আমরা দেখেছি, জেনেছি, মুখ ফিরিয়েছি। আর তাতেই জন্ম নিয়েছে আরও একটি শব, আরও একটি কান্না, আরও একটি হারিয়ে যাওয়া নাম।
আজ লিলিমা নেই। তার শরীর নেই, হাসি নেই, রান্নাঘরে কাঁসার থালার শব্দ নেই। কিন্তু সে হারিয়ে যায়নি। সে রয়ে গেছে—দুটো সন্তানের চোখে, মা ডাকের শূন্যতায়, প্রতিদিনের নিঃশব্দ অপেক্ষায়। তানিয়া এখন একটু বড়, কিন্তু মায়ের অনুপস্থিতি তাকে প্রতিদিন কিছুটা করে বুড়িয়ে দিচ্ছে। আর সুমাইয়া, যে মা’র কোলে ঘুমাতে ভালোবাসত, সে আজও ঘুম ভেঙে বলে—“মা কই?”
বার্মিংহামের সেই কমিউনিটিতে আজও অনেক লিলিমা আছেন—কেউ মুখ ফুটে বলেন, কেউ পারেন না। সমাজের অশ্রুত দেয়ালে দেয়ালে জমে থাকা কষ্ট গুলো কখনো সংবাদ হয় না, গল্প হয় না, শুধু নীরব চাপ হয়ে ঝুলে থাকে জানালার পর্দায়।
লিয়াকত এখন একটি কারাগারে। তার পায়ে শিকল, কিন্তু তার হাতে যে এক জীবন নিভে গেছে, সেই শাস্তি কোনো রায়ে পূর্ণ হয় না। আদালতের বিচার শেষ হয়েছে, কিন্তু সমাজের বিচার এখনও অসম্পূর্ণ। অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে, অনেক কান্না চেপে রাখা হয়েছে।
লিলিমার মা মুক্তাগাছায় সেই পুরনো ঘরে থাকেন। জমি এখনো তাঁর নামে। কখনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকেন, কখনো মেয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে শুধু বলেন—“এ জমি আমি রাখব, কারণ এই জমিতেই আমার মেয়ের রক্ত মিশে গেছে।”
এই গল্প কেবল একটি হত্যা নয়। এটি এক দেশের মাটির লোভ, আরেক দেশের ভাড়া ঘরের দেয়ালে ধাক্কা খাওয়া একটি নারীর জীবনসংগ্রাম। এটি অভিবাসী জীবনের সেই দিক, যেটা কখনো কারো টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে উঠে আসে না—যেখানে সফলতার আড়ালে চাপা পড়ে যায় অসমাপ্ত জীবনগুলো।